শিবলী নোমান
ব্রেক্সিট শেষ পর্যন্ত হয়েই গেলো। যুক্তরাজ্যের ৫২ শতাংশ মানুষ ইউরোপিয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে আসার পক্ষে রায় দিলেন ২৩ জুনের ঐতিহাসিক গণভোটে। বৈশ্বিক পুঁজিবাজারের সাথে সাথে বিশ্ব গণমাধ্যমও এখন ব্রেক্সিট ঝড়ে ধুঁকছে। এজেন্ডা সেটিংস-এর সহজ শিকার আমিও তাই বারংবার অনুসরণ করছিলাম ব্রেক্সিট সংক্রান্ত আলোচনাগুলো। ব্রেক্সিটের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে কী পরিবর্তন আসবে কিংবা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যে তার ফলাফল কেমন হবে তা বুঝতে পারার তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক জ্ঞান আমার পর্যাপ্ত নয়, ইচ্ছাও আছে কিনা সেটি নিয়েও ভিন্ন পরিসরে আলোচনা হতে পারে। আমার আগ্রহের পুরোটা জুড়েই আছে ব্রেক্সিটের ফলে রাজনৈতিক মহলের পটপরিবর্তনগুলো।
ব্রেক্সিট সংক্রান্ত গণভোটের আগের জনমত জরিপগুলো বলছিলো শেষমূহুর্তে উভয় পক্ষের পক্ষে প্রায় ৪৪ শতাংশ সমর্থনের কথা। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে সিদ্ধান্ত নিতে না পারা ১২ শতাংশ ভোটারের ভোটই নির্ধারণ করে দিবে যুক্তরাজ্যের ইইউ ভাগ্য। তবে ২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচনে জনমত জরিপের ফলাফলের বিপরীত ফল হওয়ায় এসব জনমত জরিপকে বিশ্বাস করা যায় কিনা সেই সন্দেহ নিয়েই এগুলোকে মস্তিষ্কে স্থান দিয়েছি তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে গণভোটের ফলাফলে জরিপ সংস্থাগুলোর উপর হয়ত যুক্তরাজ্যের মানুষের আস্থা আবারও ফিরে আসলো বা আসবে। তবে মজার বিষয় হল এই গণভোটে ভোটারদের ২৮ শতাংশ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন নি, আর দুই পক্ষের ভোটের ব্যবধান মাত্র ১৩ লাখ; দিনশেষে এই পরিসংখ্যান গণতন্ত্রের দুর্বল দিকটিকেই প্রকাশ করে গেলো। ভোটের ফলাফলে এও দেখা গেলো যে, মূলত বয়স্ক ভোটারগণ ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন যেখানে তরুনরা থেকে যেতে চেয়েছিলেন ইইউতে। তাই ভোটের ফলাফল তরুনদের জন্যে হতাশাজনক কারণ তারা কোন বাস্তবতায় জীবন কাটাবেন তা ঠিক করে গেলো তাদের পূর্বজগণ।
গণভোটে ব্রেক্সিটের পক্ষে রায় আসার পরই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ব্রেক্সিট ঝড়ের পর আসন্ন ঘটনা হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার বিষয়টি। গণভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে স্কটল্যান্ড ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ৬০ ভাগ ভোটার ব্রেক্সিটের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে ওয়েলস ও ইংল্যান্ডের সিংহভাগ ভোটার ছিলেন ব্রেক্সিটের পক্ষে। এর ফলে ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নটি গণভোটের মাধ্যমে প্রশমিত হলেও তা আবার মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে বলে মনে হয়। আবার স্কটল্যান্ড স্বাধীনতা পেয়ে গেলে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড কিংবা ওয়েলসও ঐ একই পথ অনুসরণ করবে না তা বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে ইইউর ভাঙন যুক্তরাজ্যের ভাঙনকে তরান্বীত করবে।
যুক্তরাজ্য থেকে বেরিয়ে এবার যদি ইউরোপের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, ব্রেক্সিটের ফলে ইতিমধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ডানপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলো ইইউতে থাকার প্রশ্নে তাদের দেশে অনুরূপ গণভোটের ডাক দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে অভিবাসন প্রশ্নই ব্রেক্সিটের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য। একই কথা বাকি ইউরোপের বেলাতেও সত্যি। তথাকথিত অনুন্নত ও ৩য় বিশ্বের মানুষ নিরাপদ জীবনের খোঁজে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যে গিয়েছে, উত্তর-উপনিবেশকালে এটি একটি বাস্তবতা। এর ফলে পশ্চিমা দেশগুলোতে সৃষ্ট সামাজিক সংকট, যা মূলত সরকার প্রদত্ত নাগরিক সুবিধা এবং জীবিকার সংকট হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে তা ঘনীভূত হয়েছে এবং ঘনীভূত হতে থেকেছে। কিন্তু পুরো বিষয়টি নতুন করে ইউরোপের মূল বাসিন্দাদের সামনে এসেছে নতুন করে শুরু হওয়া শরণার্থী সংকটের ফলে। এই বিপুল পরিমাণ শরণার্থীকে গ্রহণ কিংবা বর্জন বিতর্কের সাথে সাথে যারা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের দেশে মূল নাগরিকদের বিভিন্ন সুবিধা সংকোচন এবং অনেক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে পুরো পাশ্চাত্যেই অভিবাসনবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্রেক্সিটের ফলে অভিবাসনের পক্ষে থাকা সরকারগুলো একটু হলেও নড়ে-চড়ে বসেছেন কিংবা বসবেন এবং নিজেদের অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন আনবেন কিংবা আনার কথা ভাববেন তা নিশ্চিত। যদি ব্রেক্সিটের ধারাবাহিকতায় ইইউ-এর আরো কিছু সদস্য রাষ্ট্র ইইউ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আমি মোটেও অবাক হবো না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আইএস সংক্রান্ত প্রভাবের ফলে ইউরোপে সৃষ্ট শরণার্থী সংকটের ফলে ইইউ এর ভাঙন যে খুব সাধারন নয় বরং জটিল রাজনৈতিক ক্রিয়া-মিথষ্ক্রিয়ার ফলাফল তা নিয়ে ভাবতে হবে বারংবার।
চলুন আবার যুক্তরাজ্যে ফিরে যাই। যুক্তরাজ্যবিরোধী অনেকেই ব্রেক্সিটকে চিহ্নিত করেছেন যুক্তরাজ্যের ইইউকে ব্যবহারের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। তারা বলতে চান ১৯৭০ এর দশকে নিজের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে রক্ষার জন্যে যুক্তরাজ্য ইইউ-এর সাথে নিজেকে যুক্ত করে। ৪৩ বছরে নিজের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পর এখন যখন আর যুক্তরাজ্যের ইইউ-এর প্রয়োজন নেই তখন তারা গণভোটের মাধ্যমে বেরিয়ে এলো ইইউ থেকে। এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে আসুন যুক্তরাজ্য রাষ্ট্র হিসেবে কোন প্রকারভেদে পড়ে তা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলি। স্যামুয়েল পি হান্টিংটন তাঁর ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনসে চার ধরণের রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। প্রথমত, কোর রাষ্ট্র; যারা কোন একটি সভ্যতার মূল হিসেবে থাকে। দ্বিতীয়ত, ফাটলরেখার রাষ্ট্র; যেসব রাষ্ট্রে একাধিক সভ্যতা রয়েছে এবং সভ্যতার সংঘাতে এসব রাষ্ট্র খন্ডিত হতে পারে। তৃতীয়ত, একাকী রাষ্ট্র; যে রাষ্ট্রের মত সভ্যতা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আর সর্বশেষ ছিন্ন রাষ্ট্র, যারা নিজেদের চরিত্র পরিবর্তন করে। হান্টিংটন ১৯৯৬ সালে তাঁর বই প্রকাশ হওয়ার সময় ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন রাশিয়া, তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া এবং মেক্সিকোকে। কেন এগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবে সেই আলোচনায় না গিয়ে যুক্তরাজ্যেই আলাপ সীমিত রাখতে চাই। যুক্তরাজ্য গত ৪৩ বছর ইইউতে থেকেও অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা ইউরো গ্রহণ না করে পাউন্ড স্টার্লিং-কে সক্রিয় রেখেছে, গ্রহণ করেনি ইইউ এর ভিসা ব্যবস্থাও। আবার ভৌগলিকভাবে যুক্তরাজ্যকে ইউরোপ হসেবে স্বীকৃতির প্রশ্নেও দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। এসব পার্থক্যের পরও ইইউ-এর সাথে থাকার জন্যে যুক্তরাজ্যকে ইউরোপের অংশ হিসেবেই মনে হয়েছে এতদিন। কিন্তু ব্রেক্সিটের ফলে যুক্তরাজ্য কি আরেকটি ছিন্নরাষ্ট্রে পরিণত হলো কিনা তা নিয়ে ভেবে দেখার সময় হয়ে গিয়েছে। একইসাথে ব্রেক্সিটের ফলে যদি এক ইউরোপের ধারণায় ফাটল সৃষ্টি হয় এবং ফাটল তরান্বীত হয় অর্থাৎ আরো কিছু রাষ্ট্র যদি ইইউ থেকে বেরিয়ে যায় আর যদি শেষ পর্যন্ত জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনকে কেন্দ্র করে ইউরোপ থাকে তাহলে বলতেই হবে যে, হান্টিংটনের ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনে আপনাকে স্বাগতম!
ইউরোপের আলোচনায় একঘেয়ামি লাগলে আসুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চোখ ফেরাই। এটি স্পষ্ট যে ইইউ থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার পরীক্ষিত মিত্র যুক্তরাজ্যের মাধ্যমে ইইউকে নিজের প্রভাব বলয়ে রাখার চিন্তাটি আর করতে পারবে না। কিন্তু আমি অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে চাচ্ছি। মূলত্য একটি ওয়াইল্ড গেস করে লেখাটি শেষ করি চলুন। ব্রেক্সিটের ফলে ইউরোপে কোন পরিবর্তন আসুক বা না আসুক, আমার ধারণা এর সবচেয়ে বড় ফলাফল পরিলক্ষিত হবে মার্কিন প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে। এ বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য এই নির্বাচনে বিবিন্ন জরিপে হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো পিঁছিয়ে থাকলেও অভিবাসনবিরোধিতাকে সামনে রেখে ব্রেক্সিটের পক্ষে যুক্তরাজ্যের জনগণের রায় এবং ট্রাম্পের অভিনাসনবিরোধী এজেন্ডা কিংবা প্রোপাগান্ডা মিলেমিশে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করে তাহলে মোটেই অবাক হবো না। আখেড়ে, সবই তো প্রোপাগান্ডার ফলাফল!
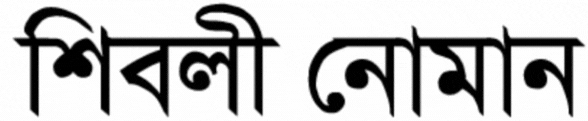

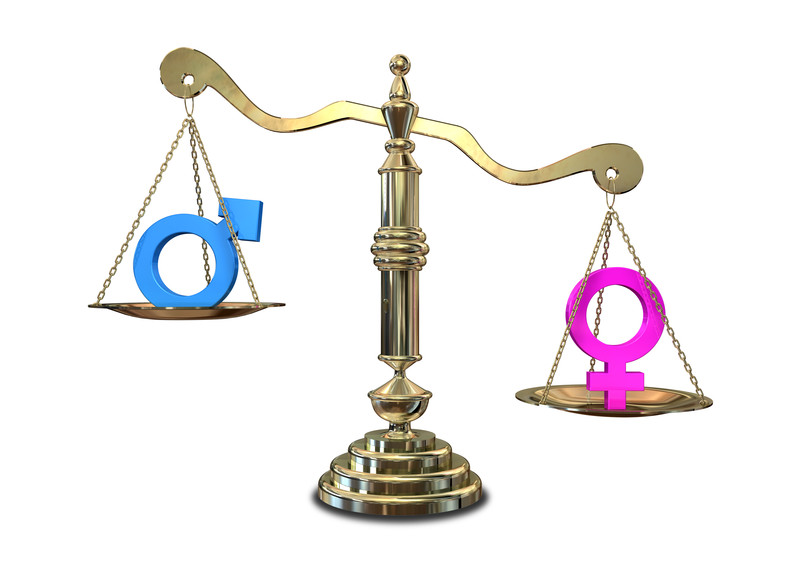
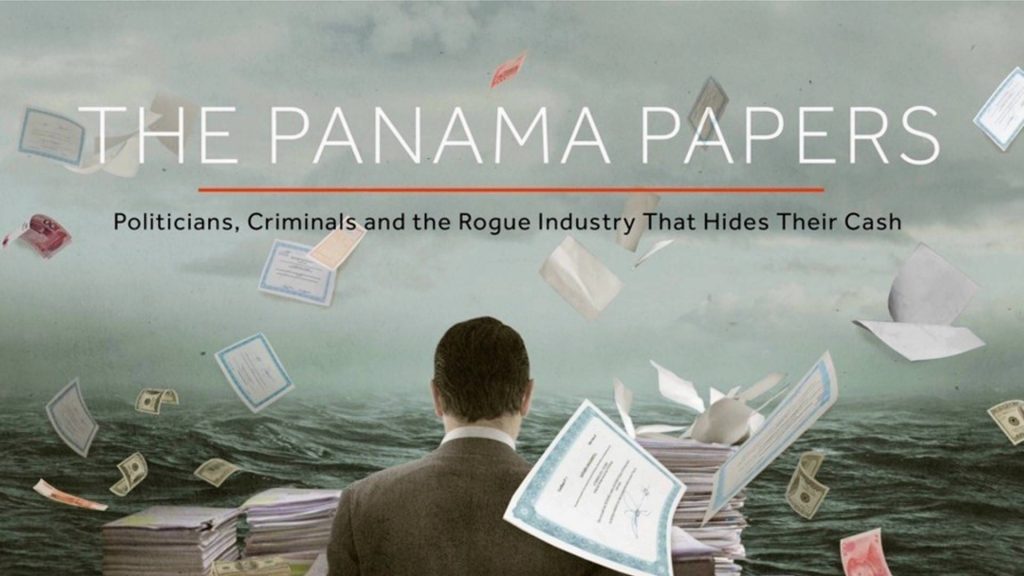
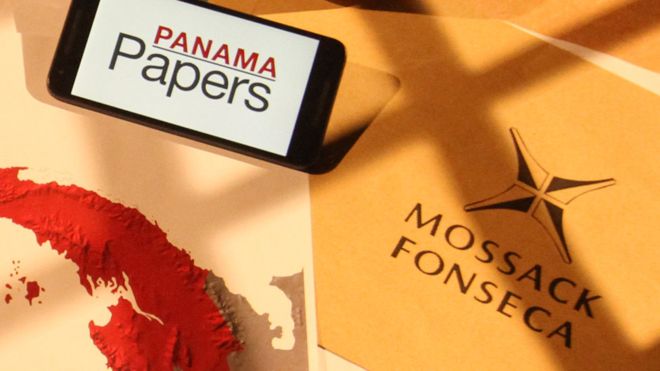
Pingback: কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা এবং সভ্যতার সংঘাতের পুনর্পাঠ