শিবলী নোমান
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সংঘটিত কোটা সংস্কার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত ফলাফল কী এবং এর ফলভোগীই বা কারা, তা নিরূপনের সময়টি যে বেশ দূরবর্তী একটি বিষয়, ইতিহাসের শিক্ষা থেকে এমনটা বলা যেতেই পারে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সর্বশেষ এই গণআন্দোলন ও এর ফলাফল যেন বেহাত হয়ে না যায়, সেই কারণে তাৎক্ষণিকভাবে এই গণআন্দোলনের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ জরুরি। যে কোন গণআন্দোলনের মতো ২০২৪ সালেও আমরা বিভিন্ন মত-পথ-আদর্শের মানুষকে এক কাতারে সারিবদ্ধ হতে যেমন দেখেছি, একইভাবে আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন মত-পথের এই মানুষদের সাংস্কৃতিক চর্চা ও তার বহিঃপ্রকাশের এক সম্মিলিত প্রয়াসও দেখা গিয়েছে প্রতিনিয়ত।
আমরা যদি আন্দোলন পূর্ববর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরের বাস্তবতা বিবেচনায় নেই, তাহলে বলতেই হবে যে এই আন্দোলনে এসব সাংস্কৃতিক চিহ্নাদির বহিঃপ্রকাশের মাত্রাটি ছিল বিধ্বংসী। নতুন কিছু ঘটার মুহূর্তের ভেতর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্টুন ও মিম প্রকাশ, খোলা প্রাঙ্গণে সম্মিলিত কণ্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশন, আন্দোলনকে কেন্দ্র করে র্যাপ গান, উপন্যাসের সংলাপ, রাজনৈতিক নেতাদের উক্তিকে সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক করে তুলে আনার মধ্য দিয়ে বিষয়গুলো দৃশ্যমান হয়। সাংস্কৃতিক চর্চার এসব উপাদানের এহেন ব্যবহারকে ‘বিধ্বংসী’ তকমা দেয়ার কারণ হলো, কোটা সংস্কার আন্দোলনে নির্বিচারে গুলি চালানোর পর তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়ার আগে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভেতর রাষ্ট্রীয় নজরদারি ও তার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় রোষানলে পড়ার যে ভীতি কাজ করতো, সেই হুমকিকে একরকম বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই সাধারণ মানুষ তাদের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। ভিন্ন আঙ্গিক থেকে এটিও বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় নজরদারি ও দমনপীড়নের এরূপ সংস্কৃতির ভেতর অবস্থান করেও মানুষের এমন বহিঃপ্রকাশ একদিকে যেমন তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার ফলস্বরূপ প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশ করে, একই সাথে এই প্রতিক্রিয়া দেখানোর ফলেই আন্দোলনকারী জনতার পেছনে ফিরে যাওয়ার পথটিকেও রুদ্ধ করে দেয়। ফলস্বরূপ আরো বেশি বিধ্বংসী বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ছাড়া তাদের কাছে কোন পথও থাকে না, ফলে দিনশেষে আন্দোলনটি প্রতিনিয়ত, বলতে গেলে প্রতি ঘণ্টায় নতুন করে বেগবান হয়েছিল এবং দিনশেষে রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনতার দাবির সামনে নতি স্বীকার করতে হয়েছে।
জনগণের ভাবনার বহিঃপ্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের মতো এই আন্দোলনে দেয়ালচিত্র ও গ্রাফিতির ব্যবহার শুধু চোখে পড়ার মতোই ছিল না, বরং দেয়ালগুলোর দখল নেয়ার মাধ্যমে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। আন্দোলনের গণচরিত্রটি কিছুটা ফিকে হতে শুরু করেছে অথবা অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে, এমন আলোচনা বা বিতর্কের উপস্থিতির ভেতর এই দেয়ালচিত্র ও গ্রাফিতিগুলোই সম্ভবত এখনো সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে সকলের চোখের সামনে উপস্থিত রয়েছে, যা প্রতিনিয়ত এই আন্দোলনের গণচরিত্র ও গণঅংশগ্রহণের দিকটিকে প্রকাশ করে যাচ্ছে।
যেহেতু প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে গ্রাফিতির কিছু স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ২০২৪-এর আন্দোলনের বহু ‘গ্রাফিতি’-কে সেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আদৌ গ্রাফিতি বলা যায় কিনা তা নিয়ে এক ধরনের বিদ্যায়তনিক বিতর্কও দেখা গিয়েছে, তাই আলোচনার সুবিধার্থে ও বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য এই রচনায় শুধুমাত্র দেয়ালচিত্র শব্দটির ব্যবহার অধিকতর নিরাপদ হতে পারে, যার অধীনে দেয়ালচিত্র, দেয়াললিখন ও গ্রাফিতি – স্বীকৃত বা অস্বীকৃত – সবকিছুই স্থান পাবে। আন্দোলনের এসব দেয়ালচিত্রে আমরা যেমন রাজনৈতিক নেতাদের উক্তি উঠে আসতে দেখেছি, তেমনি দেখেছি এই আন্দোলনে শহীদদের মুখচ্ছবি ও বক্তব্যকে তুলে ধরতে। আমরা যেমন দেখেছি গণসঙ্গীতের চরণ, একই সাথে দেখেছি এমন ভাষায় ভাবনার বহিঃপ্রকাশ, তথাকথিত সভ্য সমাজে যার প্রকাশ্য ব্যবহার গর্হিত কর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। আমরা যেমন দেখেছি দারুণ শিল্পমান সমৃদ্ধ দেয়ালচিত্র, একই সাথে দেখেছি একেবারে কাঁচা হাতে আঁকা ও লেখা অপরিণত সব দেয়ালচিত্র। অর্থাৎ এই আন্দোলনে দেয়ালচিত্রসমূহের এরূপ বৈশিষ্ট্য থেকেই আসলে আন্দোলনটির গণচরিত্র দৃশ্যমান ও প্রমাণিত হয়ে ওঠে।
এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, প্রাযুক্তিক অগ্রগতির এই কালে এবং মোটাদাগে জেন-জি সদস্যদের বৃহৎ অংশগ্রহণের এই আন্দোলনে দেয়ালচিত্রের মতো আদি মাধ্যম – যা আবার কার্টুন বা মিম তৈরির তুলনায় ব্যয়বহুলও বটে – কেন এতটা ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হলো? এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র আন্দোলনের গতিবেগের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বিস্তৃতি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এই বিষয়টিকে আমাদের দেখতে হবে দেশের রাজনৈতিক গণপরিসরের এক পুনরুদ্ধার প্রকল্পের সচেতন বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।
এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিসরে দেয়াললিখন বা ‘চিকা মারা’ বহুল প্রচলিত এক প্রকাশ মাধ্যম। কিন্তু গত দেড় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরের যে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠছিল, সেখানে দেয়াললিখন তথা দেয়ালগুলো মূলত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও দলের সর্বময় অধিকারে ছিল। আমরা নিশ্চয়ই ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকার বেইলি রোড এলাকায় গ্রাফিতি আঁকার সময় ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষার্থীদের পুলিশি হয়রানির কথা ভুলে যাই নি, কিংবা ভুলে যাই নি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়ালচিত্র মুছে গ্রাফিতি আঁকাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসনবিরোধী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টাটিও। এই সময়কালে আমরা দেখেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেয়াল কীভাবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একচ্ছত্র অধিকারে চলে গিয়েছিল। একটি দেয়ালচিত্রের উপর নতুন দেয়ালচিত্র আঁকার আগে পূর্বের কাজটি যারা করেছেন, তাদের সাথে কথা বলে নেয়ার কিংবা দেয়ালগুলো নিজেদের ভেতর ভাগ করে নেয়ার যে সাধারণ রাজনৈতিক সৌজন্য একসময় বিদ্যমান ছিল, এ ধরনের আধিপত্যবাদী চর্চার ফলে তা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা হারিয়েই হয় নি, বরং এক্ষেত্রে অত্যন্ত হীন স্বার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও অপব্যবহার করা হয়েছে। ভিন্নমতের কোন দেয়ালচিত্র দেখামাত্র তার উপর বঙ্গবন্ধুর ছবিসম্বলিত দেয়ালচিত্র এঁকে দেয়া হয়েছে, যেন কেউ তা মুছতে না পারে। যেমন, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলে বিধিবহির্ভূতভাবে নির্মিত একটি দেয়াল যেন ভেঙে ফেলা না যায়, সেজন্য সেই দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। এর ফলস্বরূপ তিনটি আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের ভেতর রাতভর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং আবাসিক হলগুলোকে লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীজনদের।
অর্থাৎ ভিন্নমতের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনপীড়ন জারি রাখার পন্থা হিসেবেই রাজনৈতিক পরিসর থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য দেয়ালগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আর বিভিন্ন আইন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল এক ভয় ও নিশ্চুপতার সংস্কৃতি। কিন্তু এরূপ সংস্কৃতির কী ধরনের বিরূপ প্রভাব শাসক মহলের উপর পড়তে পারে, সে বিষয়ে আমাদের শাসক শ্রেণি ওয়াকিবহাল ছিল বলে মনে হয় না। মূলত একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্রের অধিপতিগণ নিজেদের ক্ষমতাকে নশ্বর মনে করেন না বলেই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারেন না বা হতে চান না। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে মানুষ যখন তার না পাওয়ার হতাশা, রাগ ও ক্ষোভকে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়, তখন শাসকদের প্রতি তাদের নিত্যদিনের এই নেতিবাচক মনোভাব কিছুটা দ্রবীভূত হয়। আর সেই সুযোগ বন্ধ রেখে শাসক শ্রেণি যে আদতে কিছুই অর্জন করতে পারে না, তার প্রমাণ তো ২০২৪ সালে আমরা আরো একবার আমাদের সামনেই দেখতে পেলাম।
তাই ২০২৪ এর আন্দোলনে দেয়ালচিত্রের ব্যবহারকে শুধুমাত্র দেড় মাসের আন্দোলনের নিছক এক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা খুব একটা সঙ্গত হবে না। এটি শুধুমাত্র বিগত সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি দেশের নাগরিকদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, কারণ এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর আরো অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী মাধ্যম তাদের হাতের কাছেই ছিল এবং সেগুলো ব্যবহৃতও হয়েছে। তারপরও দেয়ালচিত্রের এরূপ বিস্তৃত ব্যবহারকে বিচার করতে হবে রাজনৈতিক গণপরিসরকে কুক্ষিগত করে রাখার বিপরীতে নাগরিকদের সচেতন ও সম্মিলিত প্রতিবাদ হিসেবে। বিষয়টি তেমন না হলে, দেশের অগণিত স্থানে মাইলের পর মেইল দেয়াল জুড়ে আন্দোলনের পক্ষে দেয়ালচিত্র আঁকা হতো না। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক চর্চাকে পাশ কাটিয়ে বিগত রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে রাজনৈতিক পরিসর হিসেবে দেয়ালগুলোকে নিজ দখলে রেখেছিল, তারই বিপরীতে সম্মিলিত জনগণ তাদের প্রতিবাদটি জানিয়েছে ২০২৪ সালের আন্দোলনে ব্যাপক হারে দেয়ালচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। দখলের বিপরীতে তাই এই প্রবণতাকে পুনর্দখল বলার চেয়ে পুনরুদ্ধার প্রকল্প হিসেবেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন।
তবে, রাজনৈতিক গণপরিসরের এই পুনরুদ্ধার প্রকল্পটি নিয়ে কতটা আশাবাদী হওয়া যেতে পারে, তা তর্কসাপেক্ষ। প্রথমত, এখানে ‘গণপরিসর’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ মানুষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর একটি মাধ্যম অর্থে, যা কখনোই সকল শ্রেণির নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করে না। অর্থাৎ, বিদ্যায়তনে ‘জনপরিসর’ বা Public Sphere সংক্রান্ত যে আলোচনা রয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে একে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। কেন যাবে না তার প্রমাণও আমরা ৫ আগস্টের পর দেখেছি যখন বিভিন্ন স্থানে দেয়ালচিত্রগুলোর অংশবিশেষ মুছে ফেলা কিংবা রঙ করে ঢেকে দেয়ার একটি প্রবণতা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। তাই দিনশেষে বাংলাদেশের দেয়ালগুলোকে নাগরিকদের রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্থান হিসেবে পুনরুদ্ধারের প্রকল্পটি কতটা সফল হলো তা বলার সময় এখনো আসে নি, তাছাড়া এর উত্তরটি আসলে আরো অনেকগুলো চলকের উপরও নির্ভর করছে। কিন্তু প্রতিরোধের সংস্কৃতি তৈরি করে রাজনৈতিক গণপরিসরে পুনরায় নাগরিকদের নিজস্ব অস্তিত্ব জানান দেয়ার এই চর্চাকে এবং অস্তিত্ব জানান দেয়ার ক্ষেত্রগুলোকে পুনরুদ্ধার করার এই স্পৃহাকে আপাতত আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা ভিন্ন কোন পথ সম্ভবত আমাদের সামনে খোলা নেই।
(রচনাকাল: অক্টোবর, ২০২৪, সাহিত্য সাময়িকী মননরেখা-র জন্য; প্রথম প্রকাশ: মননরেখা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৫, পৌষ ১৪৩১, ডিসেম্বর ২০২৪)
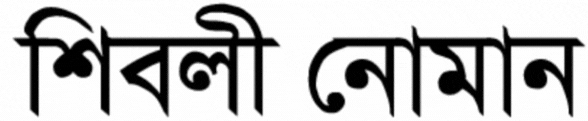

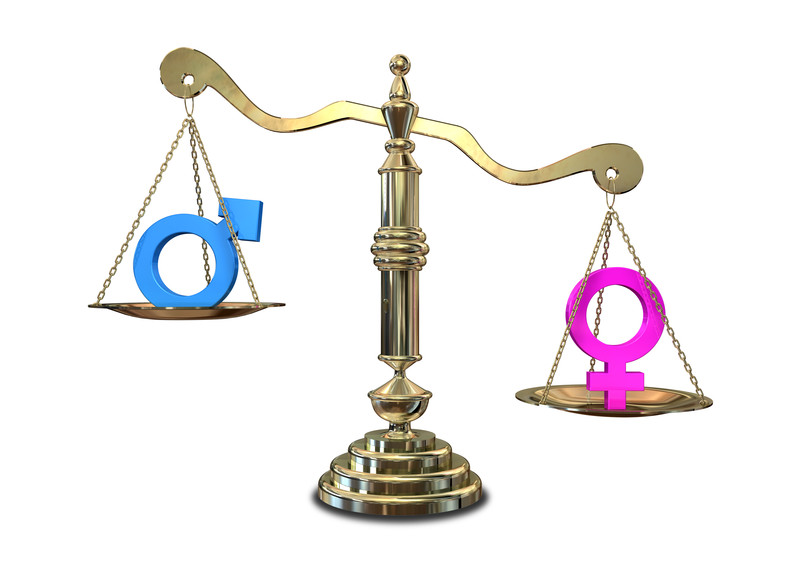
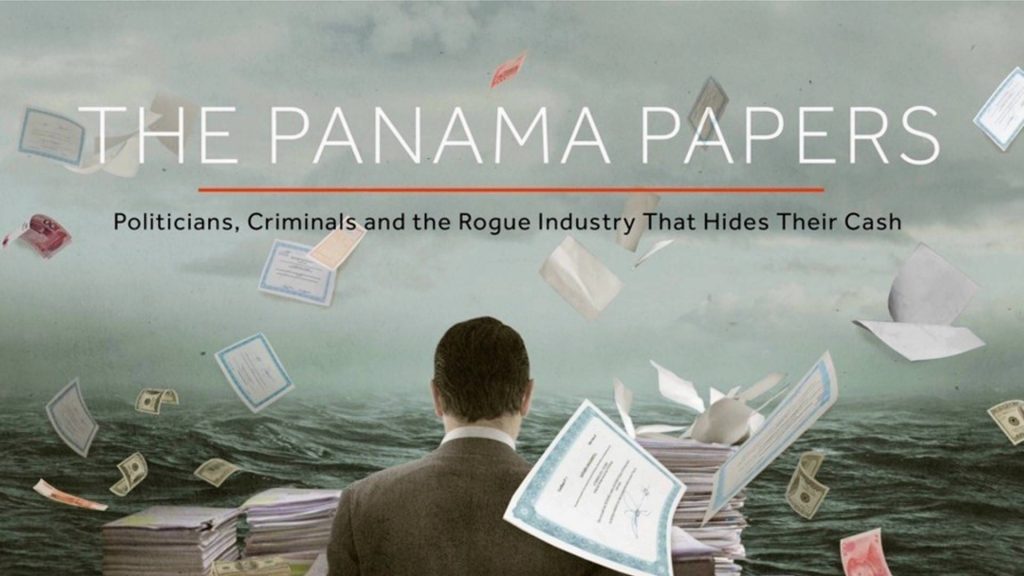
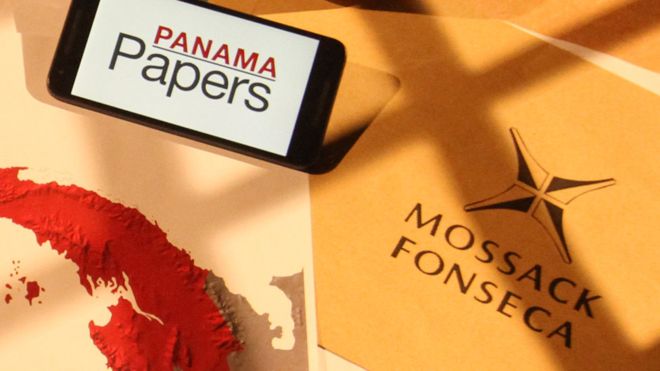
সুন্দর আলোচনা। ‘গণপরিসর পুনরুদ্ধার প্রকল্প’ পছন্দ হয়েছে প্রকাশের ধরণ।
কিছু শব্দের অতিরিক্ত দ্বিরুক্তি ভালো লাগেনি। যেমন, এরূপ/শুধুমাত্র। ‘নিশ্চুপতার সংস্কৃতি’ শব্দগুচ্ছে নিশ্চুপতা শব্দটি যথার্থ/সঠিক/এমন শব্দ আছে কিনা, সেটা নিয়ে দ্বিধা লেগেছে।
‘আমরা নিশ্চয়ই…ভুলে যাই নি’ এভাবে একটি প্রসঙ্গ লেখা হয়েছে। এখানে, স্মরণ রাখার দায়টা পাঠকের কাঁধে না দিয়েও লেখা যেতো বলে আমার মনে হয়। এই অংশটুকু পড়ার সময় মনে হচ্ছিলো, যদি আমি ভুলে গিয়ে থাকি, সেটা কি অন্যায়? ‘আমরা অনেকেই ভুলে যাই নি’ এভাবেও লেখা যেতো বলে মনে করি। (এই অংশটুকু একেবারেই আমার নিজস্ব মত। লেখকের প্রকাশভঙ্গীতে ত্রুটি খোঁজা উদ্দেশ্য নয়)
আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।